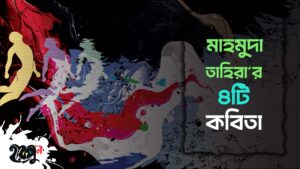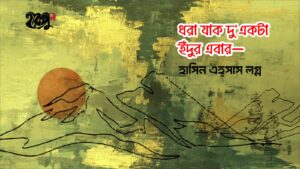কবিতা অনেক রকম। চেহারার দিক থেকে, স্বাদের দিক থেকে কিংবা বক্তব্যবিষয়ের দিক থেকে এই রকমফের। কবিতার এই বহুরূপ সাধারণ পাঠকের মধ্যে বিভ্রান্তির জন্ম দিয়ে আসছে। এরা মনে করেন কবিতা বড়জোর দু’তিন ধরনের। একজন অধ্যক্ষকে কাছ থেকে দেখেছি। ভদ্রলোক বিজ্ঞান পড়েছেন। দেশে-বিদেশে ঘুরেছেন। সাহিত্যও কিছু কিছু পড়েছেন। আধুনিক কবিতা পড়েননি বলা চলে। তাকে মন্তব্য করতে শুনেছি, ‘শামসুর রাহমানের এত নাম-ডাক। কবিতা পড়লাম। ভালো লাগেনি।’ শামসুর রাহমানই তাকে টানেনি। তিনি পঞ্চাশের প্রজন্মের একজন। তাহলে আশির বা নব্বইয়ের প্রজন্মের কবিদের কবিতা পড়লে কী রকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন এই অধ্যক্ষ মহাশয়, সহজেই অনুমান করা চলে।
সাধারণ পাঠকের মতো গড়পড়তা সাহিত্য সম্পাদকগণও (ব্যতিক্রম আছেন, কিন্তু তা খুবই বিরল) মোটামুটি মানসম্মত ‘পদ্য’কে আধুনিক কবিতা মনে করেন। ছন্দ অন্ত্যমিল দেখতে পেলে তারা খুঁশি হন। রোমান্টিক কবিতা ও আধুনিক কবিতার মধ্যকার ফারাক তারা ধরতে পারেন না। এবং কাব্য- যে অনেক রকম, এই তথ্যটি তাদের মাথায় থাকলেও পত্রস্থ করার উদ্দশ্যে কবিতা বাছাই করার সময় সেটা খুব একটা কাজে লাগে বলে প্রতীয়মান হয় না। ফলে সাময়িকী পাতায় পত্রস্থ কবিতাসমূহের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব দেখা যায়। এমন কি, ক্ষেত্র বিশেষে, এমন রচনা পত্রস্থ হয় (প্রায়শই হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি) যেগুলোকে অদৌ আধুনিক কবিতা বলা চলে না। এই অবস্থাটি গড়পড়তা পাঠকের মনে কবির প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতি সম্পর্কিত ভুল ধারণার জন্ম দিয়ে চলেছে। কেননা এক্ষেত্রে পাঠক ভাবছেন, যেহেতু বড় কাগজে ঐ ব্যক্তির লেখা নিয়মিত ছাপা হচ্ছে অতএব তিনি সুকবি। আর তা যদি না-ও হয়, মোটামুটি মানসম্পন্ন কবিতো বটেই।
এ পর্যন্ত পড়ে কারও কারও মনে হতে পারে, লেখক ধান ভানতে শিবের গীত গাইছেন। তাদের উদ্দেশ্যে সবিনয়ে বলি, উৎকৃষ্ট কবিতা লেখার সাথে যেমন পর্যবেক্ষণী দৃষ্টির যোগ অপরিহার্য, তেমনি মানসম্মত সম্পাদনার ক্ষেত্রেও এই পর্যবেক্ষণ (observation) জরুরি একটা বিষয়। যিনি সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে শ্রদ্ধেয় অথবা যে ব্যক্তি তেমন একটি জায়গা অর্জন করতে চান তাকে তো আধুনিক কবিতার (বা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার) মান এবং বিচিত্র প্রকৃতি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখতেই হবে। সেই সঙ্গে থাকা চাই সন্ধানী দৃষ্টি। আর অনুসন্ধান এবং পর্যবেক্ষণ পরস্পর নিকটাত্মীয়।
আধুনিক কবিতার ভাষা, মনে রাখতে হবে, পর্যবেক্ষণেরও ভাষা। বলার অপেক্ষা রাখে না, পর্যবেক্ষণ ব্যাপারটা কেবল আধুনিক কবিতার আওতাভুক্ত নয়। রোমান্টিক যুগের কবিতায়ও তা ছিল। ছিল আরও আগের কবিতায়। প্রাচীনকাল থেকেই বিষয়টি জড়িয়ে আছে কবিতার সঙ্গে। তাহলে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য আছে এবং সেটা পর্যবেক্ষণের ধরনে এবং ট্রিটমেন্টে। দেড় দু’শো বছর আগের কবিতায় পর্যবেক্ষণের ধরণ ছিল শাদামাটা। তার প্রকাশও ছিল সহজ-সরল ও ছন্দময়। আধুনিক যুগে কবির লেখকদৃষ্টি জটিল, মিশ্র; ফলে পর্যবেক্ষণের ব্যাপারটিও আর আগের মতো একরৈখিক ও সরল নয়। প্রাচীন কবিতা এবং আধুনিক কবিতা থেকে মোট দু’টি উদাহরণ দেবো–
অষ্টাদশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ কবি জন ডান। ডান একটি কবিতায় (ডাঁশমাছি) বলেছেন, ‘মাছি তোমার রক্ত খেয়ে এসেছে। তারপর পান করছে আমার রক্ত। তোমার রক্ত মিশে গেছে আমার রক্তে। কাজেই ভাব হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে।’
এই কবিতাটি লেখার আগে ডান অবশ্যই ডাঁশমাছির আচরণ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার বহুযুগ পরে আধুনিক কালের এক কবি সিলভিয়া প্লাথ লিখলেন, “মৌমাছিরা সবাই মেয়েমানুষ/… তারা পুরুষমানুষের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে/ মৌমাছিরা দিগ্বিদিক উড়ছে/ তারা স্বাদ নিচ্ছে বসন্তের।”
লেখা বাহুল্য, এই কবিতাটিও সৃজনের আগে প্লাথ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেছেন মৌমাছির জীবনধারা।
উৎকৃষ্ট কবিতা লেখার জন্য একজন কবিকে এই পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে হয়। কী পর্যবেক্ষণ করবেন তিনি? এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো কিছু নেই। যা- কিছু নিয়ে কবিতা লেখা সম্ভব তার সবকিছুই আসতে পারে এর আওতায়। তা হতে পারে রাস্তার প্রান্তে দাঁড়ানো সিমেন্টের খুঁটি, এমন কি একটা জং ধরা চাবিও। প্রসঙ্গত একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। একদিন গ্রামে নদীর পাড় দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ খেয়াল করি, একটা লোক কচুরিপানা সরিয়ে কিছু জায়গা ফাঁকা করে রেখেছে। ফাঁকা জায়গাগুলো গোলাকৃতি। লোকটা ঐ ফাঁকা জায়গার পানিতে কিছু একটা ছিটিয়ে দিচ্ছে। কাছে গিয়ে জিগ্যেস করি, চাচা, কি দেন?
টোয়া দেই বাবা।
‘টোয়া’ বিষয়টা বোধগম্য না হওয়ায় আবার জিগ্যেস করি, ঐ-যে পানিতে ছিটাচ্ছেন, ওগুলো কি?
এগুলি মাছের খাদ্য—- খৈল-ভুসি।
বিশ/পঁচিশ মিনিট পর ঘুরে এসে দেখি, লোকটি ঐ নির্দিষ্ট ফাঁকা জায়গাগুলোতে জাল ফেলছে। অনেক মাছ উঠছে জালে।
সে সময় আমি ছিলাম কলেজ পড়ুয়া তরুণ। পরে যখন সচেতনভাবে কবিতা লিখতে আরম্ভ করলাম তখন অনেক কিছুর পাশাপাশি ঐ ‘টোয়া’ বিষয়টিও আমাকে ভাবালো। যে কোন সময় এবং যে কোন জায়গায় ‘টোয়া’ দেয়া যাবে না। আদর্শ সময় হচ্ছে সকালের দিক এবং শেষ বিকেল। এবং সেই সব স্থান বাছাই করতে হবে যেখানে মাছের আনাগোনা বেশি। তাহলে একটা জিনিস পরিষ্কার যে, ‘টোয়া’ দেয়ার আগে জেলে ঐসব জায়গা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেন।
‘টোয়া’ দেয়ার সঙ্গে কবির কাজের অনেকখানি মিল আছে। কবিতা ধরার আগে কবিকে ‘টোয়া’ দিতে হয়। ঠিক করতে হয় তিনি কোথায় কোথায় যাবেন, কি দেখবেন আর কি নিয়েই বা লিখবেন। ওই জেলের মতো কবিকেও তার ভাবনারও পর্যবেক্ষণের জায়গাগুলো নির্ধারণ করা জরুরি। তাছাড়া ‘কি লিখবো’ এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা যেমন প্রয়োজন তার থেকেও বেশি প্রয়োজন ‘কিভাবে লিখবো’ এটা ভাবা। একজন আঙ্গিক ও শৈলিচেতন কবিকে এসব ভাবতেই হবে। আধুনিক কবির হাতে এর কোনো বিকল্প নেই।
‘কি লিখবো’ এই কথাটির সঙ্গে সঙ্গে এসে যাচ্ছে কবিতার থিমের প্রসঙ্গ। যে কোন বিষয়েই কবিতা হতে পারে। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। যে কোন মাটিতেই আপেল বা কমলাগাছ বোনা যায় কিন্তু ফলের মান সঠিক হবে তখনই যখন চারাটি সঠিক মাটি ও পরিচর্যা পাবে। তেমনি সব বিষয়ের সঙ্গে সব কবির মনের গঠন খাপ খায় না। একজন হয়তো গ্যারেজ বা লোকোশেড নিয়ে ভালো কবিতা লিখতে পারেন। আরেকজন দেখা যাচ্ছে সফল কবিতা লিখেছেন ডোবার কালো পানি নিয়ে কিংবা পানিতে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ নিয়ে। সুতরাং সৃষ্টিশীল মানুষের সৃজনইচ্ছার প্রসঙ্গে ঐ ‘মনের গড়ন’ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার।
কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলোকে আমরা কাব্যিক বিষয় বলতে পারি না। যেমন পুজিবাদের ভালো-মন্দ। এ নিয়ে চমৎকার একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ বা একটা বই লেখা যেতে পারে। অন্যদিকে, ধরা যাক অপরাজিতার ঝাড়ে প্রজাপতির আনাগোনা কিংবা মেঘলা দিনে পার্কের পরিবেশ। এগুলো থিম হিসেবে যথেষ্ট কাব্যিক। গদ্যের চেয়ে কবিতাই এসব বেশি ফলপ্রসূ হবে মনে করি। ফরহাদ মজহারের ‘এবাদতনামা’ মনে পড়লো। এই দীর্ঘ কবিতার কিছু কিছু অংশ এবং আলাদাভাবে বেশ কিছু পঙক্তি উজ্জ্বল এবং সেগুলো সজীব কবিত্বের পরিচয়বহ। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কবিতাটি মার খেয়েছে তার বিষয়বস্তুর কারণে। ধর্মচিন্তা এবং ঈশ্বরেরর অস্তিত্ব নিয়ে কথাবার্তা(কোথাও কোথাও সংশয়ও ফুটে উঠেছে) এর কেন্দ্রীয় থিম। এ বিষয়ে খুব ভালো প্রবন্ধ লেখা যেতো, লিখতে পারতেন কবি নিজেই। আমার মতে ঝুঁকিপূর্ণ এই থিম অবলম্বনে কাব্য করতে যাওয়া লেখকের সমীচীন হয়নি।
যে কোনো ক্ষমতার মতো সৃষ্টিশীল ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। কবির এটা অনুধাবণ করার প্রয়োজন আছে। কেননা তাকে তার প্রতিভামাফিক বিষয়বস্তু বা মডেল নির্বাচন করতে হবে। নচেৎ মারাত্মক ভুল হয়ে যাবে। দৃৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, খানিকটা স্বভাবকবি ধরনের একজন আধুনিক কবি, যিনি গ্রামে গাছপালার ভেতর বাস করেন এবং আধুনিক কবিতার বিবর্তন বিষয়ে যার তেমন পড়াশোনাও নাই, যদি বিউটিশিয়ান বা নগরায়ণ নিয়ে কবিতা লিখতে বসেন তাহলে তার সফল হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ তার মনের গড়নের সঙ্গে এইসব থিম খাপ না খাওয়ারই কথা। সেজন্য আমার ধারণা, এরকম ক্ষেত্রে কবির পর্যবেক্ষণ যদি থাকেও, সুফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হবে।
অল্প কিছু বিরল ব্যতিক্রম বাদে আঠারো বা উনিশ শতকের এমন কি বিশ শতকের প্রথম দিককার কবিতাও নৈর্ব্যক্তিক স্বরচিহ্নত। পরে, ক্রমশ, ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর একটা বড় জায়গা নিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে এলিয়টের কাব্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন নি, তার অবদানও বিরাট। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের, চল্লিশের, পঞ্চাশের দশকের অসংখ্য কবিতায় লেখকের এই ব্যক্তি-স্বর( personal tone) কবির স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপ,আমেরিকার কবিতার এই ধারা বাংলা কবিতাকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল; এখনো করে চলেছে সূক্ষ্মভাবে। কয়েকটি উদাহরণ দেবো।
ক. অনেক বেশি মদ খাই আমি/আমার স্ত্রী আমাকে তালাকের হুমকি দিচ্ছে/সে আমার দেখভাল করবে না/পর্যাপ্ত তৃপ্তি পাচ্ছে না সে/আমরা এক বিছানায় থাকি না।'(লাভ অ্যান্ড ফেইম,১৯৭০; জন বেরীম্যান)
খ. …শুধু জানি অনূকারে হাঁটার সময় পাথরের আড়াল/না চেয়ে আমি নিজেকে মেলাতে চেয়েছি/উজ্জল কিছুর সাথে/আর ঠিক তখন/চাঁদের শোকের সূর্যরশ্মি—তার টুকরোগুলো ছুঁয়ে গেল আমাকে— (সামথিং ব্রিলিয়্যান্ট, কাব্যগ্রন্থ: আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স, ১৯৮৬; অ্যালবার্ট গোল্ডবার্থ)
গ. চুপ থাকো প্রিয়, আর কিছু এসে যায় না আমার/ফিরে আসার জন্য অনেকগুলো গ্রীষ্ম কাটাতে হবে আমাকে :/ এই একটি গ্রীষ্মে অমরত্বে প্রবেশ করেছি আমরা/আমি অনুভব করেছি তোমার হাত দুটি/তার অমর উজ্জ্বল দীপ্তি ঢেকে ফেলেছে আমার শরীর। (দ্য হোয়াইট লিলিজ, কাব্যগ্রন্থ: দ্য ওয়াইল্ড ইরিস, ১৯৯২; লুইজ গ্লিক)
ঘ. কোনো টাইপরাইটারের শব্দ নেই এখন—দু’একটা/ভাঙা গলার স্বর/ভেসে আসছে ঘরে— এবং রাত্রির আকাশ থেকে/ঝরে পড়েছে নক্ষত্র, শব্দ নেই, শুধু মানুষ/মাদুর পেতে শুয়ে রয়েছে বারান্দায়/মশা মারছে/ বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আমি। [রাত্রি(পুরো কবিতা), কাব্যগ্রন্থ: শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা, ভাস্কর চক্রবর্তী]
ঙ. আমি ছু্ঁয়েছিলাম তার স্তন/এমন মর্মরিত নৈঃশব্দ্য আমি জীবনে ছুঁইনি/আমি ছুঁয়েছিলাম তার আঙুলগুচ্ছের অন্ধকার/এমন অসাধারণ ব্যর্থতার পাশে আর আমি দাঁড়াইনি কোনোদিন/আমি নাক ডুবিয়ে দিয়েছিলাম তার চুলে/এমন পল্লবিত গাছের ঘ্রাণ আমি আর কখনো পাইনি। (ভ্রমণকাহিনী ৪, কাব্যগ্রন্থ : শীতের রচনাবলী, আবিদ আজাদ)
উদ্ধৃত কবিতা এবং কবিতাংশগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে কতগুলো জিনিস পাঠকের চোখে স্পষ্ট ধরা পড়বে। অকপট স্বীকারোক্তি, সৃজনশীল ও চমকপ্রদ কবিকল্পনা, মানুষের অসহায়তা; আনন্দের, বেদনার কিংবা বিস্ময়ের অসাধারণ অভিব্যক্তি আছে এই পঙক্তি নিয়ে। যেমন ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের ক্ষেত্রে, তেমনি বাংলা ভাষার উজ্জ্বল কবিদের বেলায়ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রমণ্ডিত কবিতাভাষা লক্ষ করা যাচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় যা, তা হচ্ছে কবিদের নিজ নিজ পর্যবেক্ষণী দৃষ্টির সঙ্গে তাদের কাব্যে প্রযুক্ত ব্যক্তিভাষার চমৎকার মিশেল। এই ধরনের মিশ্রণ কবিতার, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে; করে চলেছে আজও। কবিরা, কি বিদেশে কি দেশে, তাদের মনের একান্ত ব্যক্তিক অনুভূতিকে যেভাবে ব্যক্তিগত উচ্চারণের বিশিষ্টতার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করে আসছেন তাতে পাঠকের পক্ষে অনেকক্ষেত্রেই সে সব রচনার মর্মোদ্ধার কঠিন হয়ে পড়েছে।
তবে ঐ ব্যক্তি-স্বরের সঙ্গে যদি কবির পর্যবেক্ষণজাত অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি সৎভাবে প্রযুক্ত হয় এবং কবির থাকে হৃদয়গ্রাহী কল্পনাশক্তি তাহলে, আমার বিশ্বাস, সেই কবির কাব্যবস্তুর শাঁসে পৌঁছে যেতে পাঠকের বেগ পেতে হবে না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, কবিতার শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। ভাবনা-কল্পনার যথার্থ প্রয়োগের ভেতর দিয়েই তা অর্জন করা সম্ভব। আর কবিতা শ্রেষ্ঠ হৃদয়শিল্প হয়ে ওঠে তখনই, যখন তা ধারণ করতে সক্ষম হয় গূঢ় ব্যক্তিঅনুভব এবং অবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণের প্রাণবন্ত ভাষা। সেই ভাষা হওয়া চাই একই সঙ্গে রসময় এবং যোগাযোগ সক্ষম। সুতরাং আধুনিক কবিতার উঁচু মান অর্জনের সাধনা একই সঙ্গে ভাষার সঠিক প্রয়োগেরও সাধনা।