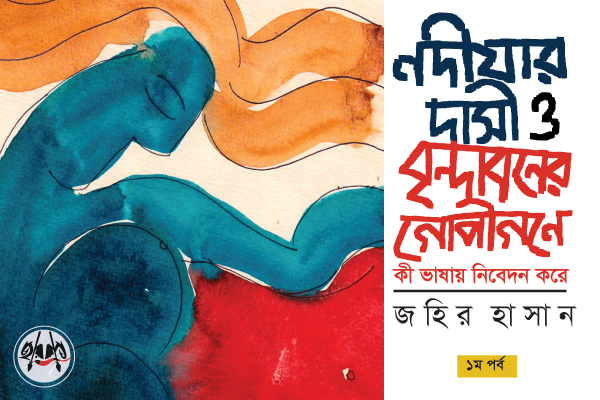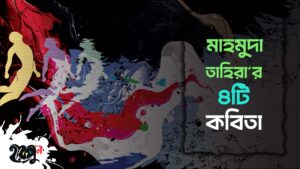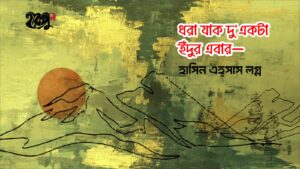কওমের ভাষায় শরীর চিন্তা ও রোমান্টিক জাতীয়তাবাদীগণের জাতীয় সাহিত্য
‘আমরা’ লিখি ও পড়ি। আমাদের অনেক বাবা, ভাই ও বোনেরা আছেন লেখেনও না, পড়েনও না। তারা শুধু শোনেন এবং মনে রাখেন। এই দুজাতের লোকের মধ্যে বিস্তর তফাৎ আছে।
আবার এক জাতের সব লোকই এক রকম নয়। যারা শোনেন ও মনে রাখেন এদের সকলেই এক নয়। এদের একটা কওম আছে। নিজের মধ্যে যোগাযোগ আছে। যোগাযোগের ভাষা আছে। যোগাযোগ অতিরিক্ত আকাজের চর্চা আছেÑ তা ভাবচর্চার শামিল।
প্রথমোক্ত লোকেরা যারা লেখেন ও পড়েন তাদের সাথে পরের যারা শুধু শোনেন ও মনে রাখেন একটা যুদ্ধ আছে, মৈত্রীও আছে।
যুগ আগাইতেছে বেধড়ক। পেটের সাথে ভাবের সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া হ”েছ প্রতিদিন। আমরা ইন্টারনেট যুগে পৌঁছে গেছি। অন্যের হাড়ির খবর আমরা অনেকে মিলে এক সাথে পর্দায় উপভোগ করতেছি।
সেই যুগের পরিসমাপ্তি বা রূপ বদলাইতেছে যে যুগে ‘গুপ্ত’ জ্ঞান ‘প্রকাশ’ বা ‘লিখিত’ যুগের কাছে হাত মিলাইতেছে।
কেউ কেউ বলতেছেনÑ না, হাত মেলানোর প্রশ্নই ওঠে না। গুপ্ত জ্ঞানধারী ভাবচর্চার লোকেরা ধারাবাহিক ভাবান্দোলন করিতেছেন। তাদের উৎপাদিত ভাব ও ক্রমাগত ‘লিখিত’ ধারার প্রকাশবাদীদের (লেখা-পড়া করে যারা গাড়িঘোড়ায় চড়ে তারা) দর্শনচর্চার মধ্যে বিস্তর ফারাক। কারণ ইহাদের উভয়ের আগাইবার মাধ্যম আলাদা। এদের কেউ বাপ-দাদার ইতিহাস ঐতিহ্যকে হারাতে চায় নাÑ তাহা লিখিয়া রাখিয়া সুপ্ত অগ্নিগিরি রচনা করতে চায়। হারাবার ভয় থেকে ভিডিও দৃশ্যচিত্রেও সকল কিছু ধরবার চায়। কারণ এরা জানে কোনো ঘাতক আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ভাবচর্চাকে চোখের সামনে হত্যা করছে। নির“পায় এই ঘাতক কে? কার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য এই তড়িঘড়ি? এই ঘাতককে বুঝবার র“খবার শক্তি আল¬াহ আমাদের দিন! আমাদের সালাত কায়েম হবে না যদি এই ঘাতক দৈত্যকে বোতলের মধ্যে না ভরতে পারি!
এই ঘাতক এক মস্ত ইরেজার হাতে নিয়ে আমাদিগকে শাসাইতেছে । সবকিছু ধসে পড়বার আগেই মুছে ফেলবার চায় সে।
এই ঘাতককে চরমভাবে চিনেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি লেখা ও পড়া জানা কওমের লোক। ‘বাঙালি’র আত্মাকে, নাড়ীকে ‘অতীত’-কে অনুভূতিযোগে ‘বর্তমান’ রূপে উৎপাদন করবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক উপ¯’াপনার খাতিরে চোখের জলে ভেসে যাই আমরা শিক্ষিত লেখা ও পড়া জানা ভদ্রলোকেরা। লেখা ও পড়া শিখে ‘অশিক্ষিত’ বাবা ও দাদার শ্র“তি নির্ভর ভাবচর্চার গভীরে তথা বাঙালির মূলের সন্ধানে নেমে গিয়েছিলেন।
শ্র“তিনির্ভর বাপ-দাদাদের চর্চাগুলানের জন্য অশ্র“বর্ষণ হৃদয়াবেগ থেকেই জাতীয় সাহিত্যের প্রতি আমাদের এতো অনুরাগ। জীবনানন্দের ‘রূপসীবাংলা’ সেই শিক্ষিতের জাতীয়ভাবকে চাগান দেয় আজও। চন্ডীদাসের কাব্য আমাদের কান্নাকে হৃদয় থেকে চোখে পৌঁছে দেয়। একটা কথা মনে রাখা দরকার সমস্যা চন্ডীদাসের নয়। জীবনানন্দেরও নয়। কারণ কেউ গায় কেউ শোনে। যে শোনে সে তার কান দিয়ে শোনে-তার দায়িত্ব বেশি । বিচারের দায়িত্বসহ শ্রোতা কিভাবে নি”েছ তা অধিকতর গুর“ত্ববহ হয়ে ওঠে । যার কান যে যেইভাবে তৈরি করছে। আর যে গায় সে তার হৃদয় কণ্ঠ দিয়েই গায়। শতফুল নিজ গুনেই ফুটে। এখন লিখিত সংস্কৃতির আর্কাইভ বানাবার যে আকুতি তার পেছনের নিহিত রাজনৈতিক অসচেতনতা আমাদেরকে অধিকতর কান্নার ভেতর ফেলবে। ফলে অধিক শোকে পাথর হয়ে আমরা কান্নাই ভুলে যাবো। যার গান তারে গাইতে দাও। যার কান্না তাকে কাঁদতে দাও। এখন এইটা করতে দিলে তো সবকিছুই মুছে যাবে। এই ভয় থেকে তাদেরে বাঁচাও। তাদেরে জীবন্ত আর্র্কাইভ বানাইয়া দাও!
ভদ্রলোকদের অতীতকালের ও বর্তমান ভাবান্দোলনের ধারাবাহিক সুতার এ-প্রান্ত-অবধি তাদের প্রতি কর“ণামিশ্রিত হৃদয়াবেগের শেষ নাই। দেরি কর না। বাপ-দাদাদের কবরগুলো পাকা করো, নইলে মাটির সাথে মিশে যাবে। জসীম উদন্ঠদীনকে দাঁড় করাও। উপ¯’াপক ও ব্যাখ্যাকারী স¤প্রদায় বুঝবার জন্য রেডি থাকো। দরদী শ্রেণী তথা শিক্ষিত ভদ্দরলোকদের ভ্রম ভাঙ্গাবার চায়। ‘মিশনারিগণ’ জ্ঞানবাতি জ্বালাইবার আগে উদ্দীপক খুঁজিতেছে।
‘শরীর’কে না বুঝলে কিছুই বুঝা যাবে না। নিকটকে না বুঝিলে ‘দূর’ ‘দিগন্ত’ ‘অসীম’কে কেমনে বুঝিবা! কারণ একজন দূূরে পৌঁছে গিয়ে আবার সেখান থেকে তাকালো পিছনেÑ যেখান থেকে সেই দূরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। পেছনের সেই বিন্দু এখন তার কাছে দূর। সে বুঝিল ‘নিকট’-এর মরীচিকা রূপই দূর। সে ভাবিল যে বিন্দু থেকে যাত্রা করেছিল সেখানেই ফিরে যাবে। সেই বিন্দুকে বুঝিলেই, স্বাদ নিলেই, দূর-অসীমের স্বাদ পাওয়া যাবে। ‘নিকট’ই শরীর।
ভাব/চিন্তা আগে, না ভাষা আগে। ব¯‘ আগে, না ভাব আগে। এহেন প্রশ্ন অবান্তর কি? ভাবের উদয়ের সাথে সাথেই তার বিপরীতে ভাষাকে কি হাজির থাকতে হয়? ভাবের বস্তুগত চেহারা টের পাওয়া যায় ভাষায়। যেখানে ভাষা নাই ভাব আছেÑ সেখানে ভাষার গরহাজিরা কে পূরণ করে ? ‘শরীর’ পূরণ করে। ‘শরীর’ তাহলে ভাষার মতো ইঙ্গিতবাহী ভূমিকায় হাজির হয়। তাই ভাষাকে দ্বিমাত্রিক একখানা সাদা কাগজের সাথে তুলনা করা চলে। একটি পাতায় থাকে দুটি পৃষ্ঠাÑ পিঠাপিঠি। একটি ভাবের আরেকটি ভাষার। ভাব ভাষায় শরীর ধারণ করে? নাকি ভাব ভাষার শরীরিক রূপলাভ করে? নাকি ভাব-ভাষা অবিমিশ্র? ভাবাক্রান্ত ভাষা যা অপরকে ভাবায় না, তখন ভাষা কি ভাবের লাশ বহনকারী হিসেবে কাজ করে? এখানে রসিকজনকে পাঠক হিসেবে গণ্য করাই শ্রেয়।
ভাব/চিন্তা আগে, না ভাষা আগে? ব¯‘ আগে, না ভাব আগে? কে গুর“তর ? ভাব না ভাষা? ভাব-ভাষা অবিমিশ্র বলে এহেন প্রশ্ন তোলা অবান্তর। ভাব ও ভাষা শব্দগতভাবে আলাদা। কিš‘ উভয়কে আলাদা করে ভাবলেই গোল। যেন রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা তবে দেহ দুই । সেইর“প রাধা ও কৃষ্ণকে দুই ভাবিলে পাপ হয়, সেইরূপ ভাব-ভাষাকে এক আত্মাধীন মনে করিতে হবে।
চোর বলিল, আমি চুরি করি নাই। কে চুরি করেছে একমাত্র আল¬াহই দ্যাখেছে। কারণ চোর জানে সে অতি সাবধানে চুরি করেছে। সবাই ঘুুমে তলাইয়া ছিল। হায় খোদা, চোর নিজের অজান্তেই নিজেকেই খোদা দাবি করিয়া বসিল। এই শরীরই সর্বহারার পৈত্রিক সম্পত্তি। এই শরীরের ভেতর যে ‘আমি’ তারে জাগাও। ‘আমি’ জাগে ‘আমিত্বের’ ধস ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। ‘আমিত্ব’ বিষয়াসক্তির লক্ষণ। শূন্য বিষয় মুক্ত। ১,২,৩… প্রভৃতি সংখ্যাদি বিষয়াসক্তির চিহ্ন। কর্তাভাব সম্পন্ন। ‘আমি’কে পাইতে হলে কাউন্ট ডাউন করে ‘শূন্যে’ (৩, ২, ১, ০) পেুৗছাতে হবে। তবেই দাস্যভাবের উদ্বোধন। তবেই জ্যান্তে মরা। তবেই আমিত্বের কারাগার থেকে ’আমি’কে উদ্ধার। পশু থেকে বিবেকী পশুকে উন্নীত হওয়া! তাই পশু ডুবিয়া ডুবিয়া জল খায় ব্যক্তির গভীরেÑ চৈতন্য খোদা সাজিয়া সংসার চালাইবার চায়। ইহাই হয়তো শরীর বিষয়ে মূল্যবান সমাচার । অন্যের দুঃখ-লাঘব করবার আগে নিজের দুঃখ লাঘবের কী কী উপায় আছে তা জানিয়া লওয়া দরকার। তাহলে অন্যের দুঃখ লাঘবের সর্বাত্মক চেষ্টা করা যাবে। কারণ এই নিজটা কে আবার? ‘অপর’ বা ‘অন্যকেউ’। কারণ আমরা ‘দূর’ ও ‘নিকট’ থেকে জানতে পারি যে, নিকটের মধ্যে দূরের খবর লুকানো থাকে। অর্থাৎ ‘দূর’ নিকট সমার্থক ও শব্দগতভাবে বিরোধার্থক। আমি যা করি আমার পুত্রের জন্য। আমার পুত্র করে প্রতিবেশির জন্য। প্রতিবেশি করে তার প্রতিবেশির জন্য। আমাকে প্রতিবেশির মাধ্যমে দেশে দেশে ছড়াইয়া দিতেছি। আমির বি”ছুরণ আমরা হয়ে ওঠে। আমিত্বের বিলোপের মধ্যেই আমির প্রসারণ। অপরের মধ্যে নিজের বিলোপ ও নিজের অপর হয়ে ওঠার মধ্যে নিজত্বের দাবি। নিকটকেই জানার মধ্যেই শরীরকে জানা যায়। আমার নিকটের প্রকৃতিকে জেনে অজান্তে তার সাথে পীরিতের বশে তাতে মজে গেলে তার ভাবানুভূূতি নিজ ‘কওমের ভাষায়’ লিখলে কিছুু দাঁড়াবে। ভাষার ইটগুলা বাপ-দাদাদের সম্পত্তি। কিš‘ মনের মতো ঘর বানাইতে হয় নিজেকেই। বিদেশি ইটে ঘর বানাইলে তা কতটুকু টিকবে তা বুঝা ভার। কারণ ঐ ইট নিয়া আমি কারবার করি নাই। তবে টিকিবার সম্ভাবনাকে উড়াইয়া দেয়াও যায় না। সাহিত্যে এক্সিট্রিমিজমের জায়গায় কম। তবে নিজ ভাষা দিয়া নিজ কওমের বিষয়ে রচনা ক্কতরি করিলে শক্ত হয় দালান এ-ব্যাপারে নজির হাজির করা দুর“হ কিছু নয়।
যে যেই ঘরে জন্ম সেই ঘরের আচার-ব্যবহার না করে অন্যথা করিলে ভড়ং হয়ে উঠতে পারে। কেউ ‘নিজের’ ভাষায় না লিখে ‘অন্যের’ ভাষায় লিখলে তা ‘ভড়ং সাহিত্য’ হয়ে ওঠে। এই নিজ জিনিসটা বুঝতে হবে। কার ভাষায় কার কথা কে বলিতেছে? এই প্রশ্ন জর“রি। উপ¯’াপনার গুণে তা অনেক সময় উৎরায়ে যায় বটেÑতবে তা ‘শরীর’ চিন্তা এলাউ করে না।
কিš‘ প্রশ্ন হ”েছ এইসব ‘পিওর’ চিন্তার দিন কি এখনো আছে? যে যে যশোর, চিটাগাং, কুমিল¬ায়, নোয়াখালী, সিলেটে জন্মাইয়া সে সে নিজ নিজ ভাষায় নিজ জীবনের ভার হাসি-ঠাট্টা তুলিয়া ধরিলে সবচেয়ে ভালো হইবে? কেননা ওটাই তার শরীর-প্রতিবেশ।
কিংবা আরও ক্ষতিকর প্রশ্ন তোলা যায় ঐ ঐ অঞ্চলের ভাষা কী বাংলা ভাষা? যারা ঐ ভাষায় সাহিত্য-রচিবেন তিনি মূলত বিদেশি ভাষাতেই সাহিত্য রচিবেন। ফলে তা ভদ্দরলোকদের মান ভাষায় অনুবাদ করেই পড়িতে হইবে। ভৈকম মুহম্মদ বশীর মালায়লম ভাষায় গল্প-উপন্যাস রচিয়াছেনÑ আমরা পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষায় অনুবাদ পড়িয়াছিÑ যাকে মনে হয় না অনুবাদ। এই রূপে অনুবাদসাহিত্যেরও পরিধি বৃদ্ধি পাবে। ‘রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই’ আন্দোলন তাহলে কী ‘মায়ের ভাষা’কে রক্ষা করিবার আন্দোলন ছিল না? নাকি শুধু মানভাষার ‘বাংলা’কে রক্ষা করিবার উদ্যোগ ছিলÑ সেদিনের ঔপনিবেশিক শক্তির বির“দ্ধে দাঁড়াইবার তাগিদে।
বিদ্যাপতি যে-ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন, তা নাকি একটি বানানো মিশ্র ভাষা। এই ভাষা কোনো কওমের ভাষা নয় কিš‘ তা সাহিত্য হিসেবে উ”চ মূল্য পাইতেছে। বুঝা যা”েছ সাহিত্য জিনিসটা শুধুই ঐতিহ্য কওমের ভাষাচিহ্নও নয়, ইহা রসালো ও ভাবালোতে উজ্জীবিত হয়েই বেঁচে থাকে।
তাই ভাষার রাজনীতি ও সাহিত্যের রাজনীতি আলাদা। ভাষা টিকিয়া না থাকলে তার সাহিত্য কিভাবে টিকিয়া থাকিবে। এই প্রশ্নে আসলে আমরা আবার থমকে দাঁড়াই, বুঝি ভাষার টিকে থাকার সঙ্গে সাহিত্যের টিকে থাকার একটা যোগ আছে। অতএব সাহিত্য ও ভাষা রাজনীতি একত্রে চলিতে হবে।
মিশ্রভাষা বা বানানো ভাষায় রচিত সাহিত্য যদি যোগাযোগ অতিরিক্ত রস ও ভাব জড়িত হয় তা উ”চ মূল্য পায় বটে তবে তা সাহিত্যের ইতিহাসের ভাষার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বা ক্রমবিকাশ হিসেবে চিহ্নিত হয় না। বিদ্যাপতি মহাশয় যে-ভাষায় কাব্য করেছিলেনÑ গোবিন্দাদাস ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষার অনুসরণে বৈষ্ণব ভাবধারায় কাব্য করেছিলেন।
রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলীর ভাষায় আর কোনো স্বাভাবিক কাব্য লেখেন নাই। ফলে রবীন্দ্রভাষার ক্রমবিকাশের আলোচনার ভানুসিংহের পদাবলী গুর“ত্ববহ কিছু নয়। কওমের ভাষা থেকে দূরে গিয়ে বানানো ভাষার সম্ভবনা আছে কিš‘ ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয় না। তবে ব্যাপকভাবে যদি কোনো লেখকগোষ্ঠী ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করে এই ভাষায় লেখেন তাও টিকে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষায় সাহিত্য রচেছেন তা ভদ্দরলোক শ্রেণীরই ভাষা। পরবর্তীতে ঐ ভাষাই তথাকথিত মেইনস্ট্রিম সাহিত্যভাষা আকারে জারি হয়েছে। রাষ্ট্রও ঐ ভাষাকে আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছে। পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অনেক রোদন করেছেন এই বলে যে তিনি মাটির কাছাকাছি যেতে পারেন নাই। তার এই রোদনকে আমরা সিরিয়াসলি নিই নাই। তার রোদনের মধ্যে আমাদের পাথেয় নিহিত ছিল। যা হোক রবীন্দ্রনাথ তার ভাষাগোষ্ঠী, তার কওমের ভাষাকে নিয়েছিলেন। ভদ্দরলোকদের কৃত্রিম ভাষাই রবীন্দ্র কওমের ভাষা। সেই অর্র্থে রবীন্দ্রনাথ সার্থক। কিš‘ আমরা যারা সাহিত্য করিতেছি তারা কি তার কওম লয়ে ভাাবিত? অতি ভালোবাসার সঙ্গে রাজনীতি জড়িত। স্বাভাবিক ভালোবাসার সঙ্গে রাজনীতি নুনে জলে নিশে থাকে। কওমের ভাষাকে জাতীয় আকার লাভ করানোর ক্ষমতা বড়ই আশ্চর্য। রাষ্ট্র যদি নিজে ঐ ভাষায় কথা বলে তবেই সম্ভব। জাতীয় ভাষা ও জাতীয় সাহিত্য এই দুয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান আছে। জাতির জীবন-যাপন, স্বভাব-চরিত্র ও ভাব যে সাহিত্যের মালমশলা তা জাতীয় সাহিত্য হতে পারে। যেখানে বাংলাদেশের আশিভাগ লোক গ্রাম জীবনের স্বাদ নিতেছেন। তাদের বিবিধ বিষয় যখন সাহিত্য অধিকার করে তখন তা জাতীয় সাহিত্য হইতে পারে। তাহলে শহুরে সাহিত্য বিপরীতে পয়দা হয়। নিখাদ ‘সাহিত্য’ জিনিসটার খোঁজে বের হওয়া তখন বেহুদায়। ‘লোক-সাহিত্য’, ‘মুসলামন-সাহিত্য’ যেভাবে ভাগ করা হয়। ফের রাজনৈতিকভাবে আগাইয়া থাকা মেইনস্ট্রিম সাহিত্যই সাহিত্য। শ্রুতি-নির্ভর সাাহিত্যের ইতিহাস নাই। অতএব উহার ভাব নিয়া যে আন্দোলনÑতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যারা ইতিহাস তৈরি করে বা লেখে তারাই সাহিত্যের কর্তা। কিংবা নিচে থেকে ইতিহাস না লেখায় শ্র“তিনির্ভর সাহিত্যের নায়েকেরা বাদ পড়ে উঁচু থেকে লেখা ইতিহাসবিদদের তালিকা থেকে। যার কারণেই ‘হিন্দু সাহিত্য’ বলে কিছু নাই। ‘মুসলিম-বাঙলা সাহিত্য’ বলে কিছু আছে। কথ্য আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য রচনাও মিশ্র ভাষায় সাহিত্য রচনার চিন্তা বর্তমান সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ’৪৭ ও ’৭১ পরবর্তী বাংলাদেশের বাংলা ভাষার যে অব¯’া তা পশ্চিম বাংলার ভাষা থেকে নিশ্চিত ভিন্ন হয়ে গেছে। যারা নিজেকে আঞ্চলিক বা বৃহতের ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে ভাবছেন তারা বৃহৎ মূলত ক্ষুদ্র অংশ তথা রাষ্ট্রের ভাষা আধিপত্যকেই স্বীকার করে নি”েছন। ফলে মান ভাষার কাণ্ডারি ও আঞ্চলিক ভাষার মাঝি উভয়ের বিবাদ ফয়সালা হয় না। দুপক্ষের কেউ কাউকে স্বীকৃতি দেয় না। মাঝখানে মিশ্র ভাষায় লেখা সাহিত্য ও উভয় দলের কেউ না যেন সাধারণ হয়ে উঠছেন। সেতু রচনা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কতটুকু নতুন দিকে নেয়া যায় সেই চিন্তা করছেন। সমন্বয়বাদী এই চিন্তা আমাদের কাব্য সাহিত্যে অনেক বাঁক তৈরি করবে হয়তো। তার দর্শক আমরা মধ্যবিত্তরসিকগণ উৎসাহিত হইবো।
অধ্যাপক দীপেশ চক্রবর্ত্তী কর“ণামিশ্রিত সাব-অলটার্নপ্রীতিকে ‘রোমাণ্টিক জাতীয়তাবাদ’চর্চার সামিল মনে করেন। রোমাণ্টিক জাতীয়তাবাদীদের নিকট কর“ণামিশ্রিত সাব-অলটার্নপ্রীতির শেষ নাই। এরা ‘নিকট’কে নিকট থেকে দেখে না নিকটকে দূর থেকে দেখে। ফলে নিকট/দূর এই ‘নিকট’ দূরেই থেকে যায়Ñ দূূর নিকটের ভেতর ঘুমায়। রোমাণ্টিক জাতীয়তাবাদীরা শহর থেকে স্বপ্নে জাগরণে গ্রাম কালচারে লংমার্চ করে। যেনো সে শহরে ফিলিস্তানি জীবন-যাপন করছে। মধ্যবিত্তের রোমাণ্টিক সংস্কৃতিচর্চা বড়ই আনন্দের। আহমদ ছফা দীনেশচন্দ্র সেন স্মরণে মজার জিনিস উদ্ধার করেছেন। ‘সমর সেনের (দীনেশচন্দ্র সেনের নাতি) স্মৃতিকথায় দীনেশ সেন সম্পর্কে আমরা মাত্র দুুটি প্রধান তথ্য জানিতে পারি। সেটা হল, দীনেশ সেন একবার সময় সেনকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, নাতি তোমার সঙ্গে একটা বড়লোকের মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছি। তারা তোমার বিলেত যাওয়ার খরচ দেবে। নাতি জবাব দিয়েছিলেন, দাদা মশাই কাজটা আপনি ঠিকই করেছেন; কিš‘ আমি পুর“ষাঙ্গ বন্ধক দিয়ে বিলেতে যাব না।’
দীনেশচন্দ্রের ‘বৃহৎ বঙ্গ’ ও ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ যে-সব রেফারেন্সগুলো নিয়ে কথা বলেছেন তা একশ ভাগ খাঁটি। দীনেশের ক্রন্দনে আমাদের সে বিষয়ে কিছু আগ্রহ বৃদ্ধি পায় বটে।
আইকন দীনেশ সেনকে দিয়েই আমরা বাঙালি মধবিত্তের সাহিত্যচর্চার রগকে ধরতে পারি। সাব-অলটার্ন জীবনের প্রতি আমাদের কর“ণ টানÑ ঈশ! ময়মনসিংহ গীতিকার নায়িকার মতো কোনো নায়িকা কী নাতির জন্য বেছে নেওয়া যেত না! দীনেশ বাবুর চর্চার বিষয় এক জীবন-যাপন বাসনার জায়গা আর একÑ (যাক, তবু তিনি ফ্যান্টাসিকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য জোরাজুরি করেন নাই !) এই যে ফারাক! বড়লোকের সাব-অলটার্নচর্চাÑ অন্যের ভাগ্য, পরিবর্তনের জন্য আহারে ক্রন্দন!